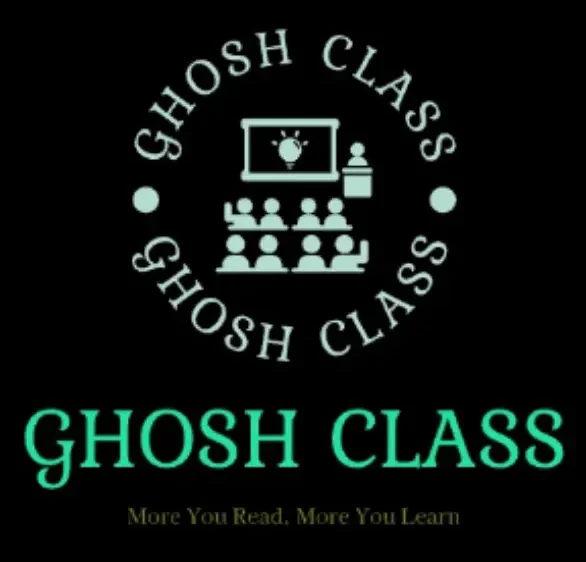প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো।
বিকল্প উত্তর: ১
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো।
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন, কেউ জাতীয় বিদ্রোহ, আবার কেউ বা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া কিংবা ষড়যন্ত্র।
সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা:
বেশিরভাগ ব্রিটিশ লেখক যেমন স্যার চার্লস রেকস, জন সিলি, আর্ল রবার্টস প্রমুখ ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন।
ভারতের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজি, অক্ষয় কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও এই মতের প্রতি সহমত পোষণ করেছেন।
ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857’ গ্রন্থে বলেন:
এই বিদ্রোহের পিছনে কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না।
বিপ্লবীদের মধ্যে লক্ষ্য ও ঐক্যের অভাব ছিল।
শতবার্ষিকীতে তিনি বলেন:
“The so-called First National War of Independence in 1857 is neither First, nor National, nor War of Independence.”
জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা:
অনেকেই একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।
ডিসরেলি, নর্টন, ডাফ, হোমস প্রমুখ এই বিদ্রোহকে জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।
বিনায়ক দামোদর সাভারকর একে “ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ” বলে চিহ্নিত করেন।
তাঁদের যুক্তিগুলি হল:
পূর্ববর্তী আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলির তুলনায় এই বিদ্রোহে ব্যাপক গণসমর্থন দেখা গিয়েছিল।
সুরেন্দ্রনাথ সেন উল্লেখ করেন, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহটি এক জাতীয় রূপ পায়।
সামন্ত বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা:
রজনীপাল দত্ত, এরিখ স্টোকস, জওহরলাল নেহেরু, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ইতিহাসবিদরা একে একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।
জওহরলাল নেহেরু তাঁর ‘Discovery of India’ গ্রন্থে একে সনাতনপন্থীদের বিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
ষড়যন্ত্র তত্ত্ব:
ব্রিটিশ সেনা-জেনারেল আউট্রাম এই বিদ্রোহকে “মুসলমানদের ষড়যন্ত্র” বলে আখ্যা দেন।
তাঁর মতে, মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন।
সমালোচনামূলক মূল্যায়ন:
এই বিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও একে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না।
যদিও শিখ, গোর্খা, রাজপুত প্রভৃতি গোষ্ঠী এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি, তবুও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও জন-অংশগ্রহণ একে একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের চেহারা দেয়।
সুশোভন সরকার বলেন:
“হজরত মহল, কুনওয়ার সিং, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ সামন্ত জমিদারদের নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও একে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ বলা যায় না।”
এই বিদ্রোহে উপস্থিত গণচরিত্র, ধর্মীয় সংহতি, এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ-এর প্রকাশ ভারতের জাতীয়তাবাদের বীজরোপণ করে।
উপসংহার:
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একাধিক মাত্রায় ব্যাখ্যাত। একে সামরিক অভ্যুত্থান, ষড়যন্ত্র, সামন্ত বিদ্রোহ কিংবা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম — যেভাবেই দেখা হোক না কেন, ভারতীয় ইতিহাসে এ বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আকারের প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।
বিকল্প উত্তর: ২
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো।
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন, কেউ জাতীয় বিদ্রোহ, কেউ স্বাধীনতা সংগ্রাম, কেউ বা গণবিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
(১) সিপাহী বিদ্রোহ মতবাদ:
অনেক ঐতিহাসিক যেমন চার্লস রেইকস, জন কে, সৈয়দ আহমেদ খান, কিশোরী চাঁদ মিত্র, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ এই বিদ্রোহকে নিছক সিপাহীদের বিদ্রোহ বলেছেন। তাদের মতে:
বিদ্রোহটি শুরু হয় সিপাহীদের মাধ্যমে এবং তাদের স্বার্থেই ছিল।
দেশীয় রাজারা নিরপেক্ষ ছিলেন বা ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিলেন।
সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত সমাজ এই আন্দোলনে অংশ নেয়নি।
(২) জাতীয় বিদ্রোহ মতবাদ:
ম্যালেসন, জে.বি. নর্টন, কার্ল মার্কস প্রমুখের মতে এটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না। তাদের যুক্তি:
পরে বিভিন্ন শ্রেণির অসামরিক মানুষ বিদ্রোহে যোগ দেন।
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ‘ভারতের সম্রাট’ ঘোষণা করা হয়।
বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসন অবসান করা, তাই এটি জাতীয় বিদ্রোহ।
(৩) প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম মতবাদ:
বিনায়ক দামোদর সাভারকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পি.সি.জোশি প্রমুখ এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছেন। কারণ:
ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিবাদ এতে প্রতিফলিত হয়।
বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিতাড়নের লক্ষ্যে একজোট হয়েছিল।
এটিই ছিল প্রথম বৃহৎ ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন।
(৪) গণবিদ্রোহ মতবাদ:
সুরেন্দ্রনাথ সেন, জন কে প্রমুখের মতে:
পশ্চিম বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিদ্রোহ ছড়ায়।
কৃষক, শ্রমিক, কারিগরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।
তাই একে গণবিদ্রোহ বলা যায়।
(৫) সামন্ত বিদ্রোহ মতবাদ:
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. রজনীপাল দত্ত প্রমুখের মতে:
এটি ছিল সামন্ত শ্রেণির ‘মৃত্যুকালীন আর্তনাদ’।
কিন্তু অনেক সামন্তই ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল বলে এই মত বিতর্কিত।
(৬) আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত:
ড. হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ড. রণজিৎ গুহ, ড. রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বলেন:
সাধারণ মানুষ শুধু অংশগ্রহণ করেননি, নেতৃত্বও দিয়েছিলেন।
এরিক স্টোকস বলেন, এই বিদ্রোহ ছিল নানা ধারার মিলন – যেমন কৃষক বিদ্রোহ ও জাতীয় প্রতিরোধ।
উপসংহার:
১৮৫৭-র বিদ্রোহ একক স্বরযুক্ত ছিল না, বরং ছিল বহু শ্রেণির অংশগ্রহণে গঠিত এক সম্মিলিত প্রতিরোধ। তাই একে কেবল সিপাহী বিদ্রোহ না বলে একটি বহুমাত্রিক গণপ্রতিক্রিয়া বলা অধিক যুক্তিযুক্ত।
বিকল্প উত্তর: ৩
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো।
উত্তর: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এর প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। কেউ একে সামরিক বিদ্রোহ, কেউ জাতীয় বিদ্রোহ, আবার কেউ কেউ একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।
১. সামরিক বিদ্রোহ হিসেবে:
অনেক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক যেমন স্যার জন লরেন্স, জন সিলি ও চার্লস রবার্টস এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় সমকালীন চিন্তাবিদ আলোককুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মিশোরীচাঁদ মিত্র-ও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন।
তাঁদের মতে—
(i) বিদ্রোহের সূচনা সিপাহিদের হাত ধরে হয় (মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনা)।
(ii) এর পেছনে কোনও সুসংগঠিত রাজনৈতিক চিন্তা বা নেতৃত্ব ছিল না।
(iii) সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত।
২. জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে:
ঐতিহাসিক নটন, আউট্রাম, ম্যালেসন ও ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ডিসরেলি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন।
তাঁদের মতে—
(i) ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, কুয়র সিং প্রমুখ রাজন্যবর্গ এতে নেতৃত্ব দেন।
(ii) তালুকদার, জমিদার ও সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে এতে অংশ নেন।
(iii) দিল্লির সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে জাতীয় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
(iv) রজনী গুপ্ত ও সুশোভন সরকার-ও একে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসেবে গণ্য করেন।
৩. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে:
বীর সাভারকার প্রথম এই বিদ্রোহকে “ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ” বলে আখ্যায়িত করেন। তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ড. শশীভূষণ চৌধুরী এর বিরোধিতা করে বলেন—
(i) বিদ্রোহটি দেশব্যাপী ছড়ায়নি; পাঞ্জাব, বাংলা ও দক্ষিণ ভারত ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়।
(ii) অনেক রাজা-মহারাজা ইংরেজদের সহযোগিতা করেন।
(iii) বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল অস্পষ্ট ও বিক্ষিপ্ত।
(iv) এটি এককভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়নি।
৪. সামন্ত বিদ্রোহ হিসেবে:
ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, জওহরলাল নেহরু, রজনী পাম দত্ত ও এস. এন. বস-এর মতে—
(i) এটি ছিল পুরনো সামন্ত ও জমিদার শ্রেণির প্রতিরোধ।
(ii) ইংরেজ শাসনের অধীনে আধুনিক প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিক্রিয়া।
৫. গণ-বিদ্রোহ ও মূল্যায়ন:
বামপন্থী ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুশোভন সরকারের মতে—
(i) এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিদ্রোহ।
(ii) শ্রেণি বিভাজন থাকা স্বাভাবিক, তবে এটি জাতীয় চরিত্র অস্বীকার করে না।
(iii) এটি ভারতের জাতীয় চেতনার প্রাথমিক প্রকাশ।
উপসংহার:
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল একটি বহুমাত্রিক ঘটনা—সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও এর সূচনা সিপাহিদের দ্বারা হয়, পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এটি এক জাতীয় চেতনার রূপ নেয়। সুতরাং, একে কেবল সিপাহী বিদ্রোহ বলা সঠিক নয়; বরং এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি।
বিকল্প উত্তর: ৪
প্রশ্ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎসার্বভৌম প্রতিবাদ বলে বিবেচিত হয়। যদিও এর আগে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিদ্রোহ হয়েছিল, ১৮৫৭-র এই বিদ্রোহ ছিল সেই প্রথম আন্দোলন যা জাতীয় চরিত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।
এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ একে সামরিক অভ্যুত্থান, কেউ বা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, কেউ ষড়যন্ত্র, কেউ কৃষক বিদ্রোহ, আবার কেউ একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন।
১. সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে ব্যাখ্যা:
ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস রেক্স, রেল আউট্রাম ও ডব্লিউ টেলরসহ অনেকেই এই বিদ্রোহকে সিপাহীদের অসন্তোষের ফল বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মত সমর্থন করে বলেন যে বিদ্রোহটি মূলত সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও কিছু এলাকায় এটি জনজাগরণের রূপ নেয়।
২. সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে:
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ড. সুশোভন সরকার বিদ্রোহটিকে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শেষ চেষ্টা হিসেবে দেখেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, স্থানীয় রাজাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা এবং পাশ্চাত্য সংস্কারের বিরোধিতা এর মধ্যে স্পষ্ট।
৩. ষড়যন্ত্র তত্ত্ব:
ম্যালসন ও অধ্যাপক কি (Key) বিদ্রোহটিকে একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, আহমদুল্লা, ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই, ও নানা সাহেব মিলিতভাবে একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করেন।
৪. কৃষক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ:
টমাস ইভানস বেল বিদ্রোহকে কৃষকদের দীর্ঘদিনের জমি ও খাজনা-সংক্রান্ত অসন্তোষের পরিণতি বলে মনে করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়, যা তাদের বিদ্রোহে নামতে বাধ্য করে।
৫. প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে:
ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, এস. বি. চৌধুরি, ড. তারাচাঁদ, সাভারকার প্রমুখ এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, এটি কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়, বরং ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধ। কার্ল মার্কসও একে “জাতীয় বিদ্রোহ” বলে অভিহিত করেছেন।
ড. সুশোভন সরকারের মতে, যদিও বিদ্রোহকারীদের কোনো সুসংহত রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না, তথাপি বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণ এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জাতীয়তাবোধের প্রকাশ ঘটায়।
উপসংহার:
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি বহুমাত্রিক। একদিকে এটি ছিল সিপাহীদের অসন্তোষের ফল, আবার অন্যদিকে সামন্ততন্ত্র, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই বিদ্রোহ ভারতের জাতীয় চেতনার সূচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।
আরও দেখো: একটি গ্রামের মেলা রচনা