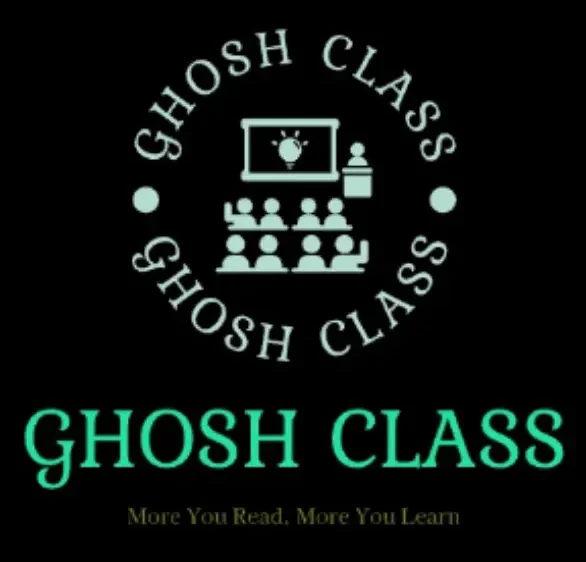এখানে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) থেকে প্রশ্ন উত্তর শেয়ার করা হলো। / ক্লাস 8 বাংলা
অষ্টম শ্রেণী বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
বিষয়সংক্ষেপ
“জেলখানার চিঠি” হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা একটি পত্র, যা তিনি মান্দালয় জেল থেকে তাঁর প্রিয় বন্ধু সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়কে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তারিখে লিখেছিলেন।
চিঠির শুরুতেই তিনি দিলীপকুমার রায়ের পূর্ববর্তী চিঠি প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং খুশি প্রকাশ করেছেন যে সেটি কোনো বাধা ছাড়াই তাঁর হাতে পৌঁছেছে। এরপর তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতের কারা-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করে ভবিষ্যতে কারা-সংস্কারকে নিজের কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের উচিত আমেরিকার মতো উন্নত দেশের কারা-ব্যবস্থা অনুসরণ করা, যেখানে প্রতিষেধমূলক নয় বরং সংস্কারমূলক দণ্ডবিধি কার্যকর।
নেতাজির মতে কারাবাসের অভিজ্ঞতা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মানসিকতা ও সৃষ্টিশীলতাকে সমৃদ্ধ করে। তিনি উদাহরণ হিসেবে নজরুল ইসলামের সাহিত্য এবং লোকমান্য তিলকের গীতার আলোচনা রচনার কথা বলেছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে মান্দালয় জেলের দুঃসহ পরিবেশই তিলকের অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ।
চিঠিতে নেতাজি স্পষ্ট করেছেন, কারাবাস মানুষকে দর্শনচিন্তা ও আত্মসমালোচনার সুযোগ দিলেও জেলের অপশাসন বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ডেকে আনে। বন্দিদের অকালবার্ধক্য রোধে তিনি সঠিক খাদ্য, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সংগীতচর্চা ও পিকনিকের আয়োজনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দিদের জন্য সাপ্তাহিক সংগীতচর্চার ব্যবস্থার কথাও তিনি স্মরণ করেছেন।
তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক বন্দিরা সমাজে সম্মান পায়, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের প্রতিও সমাজের সহানুভূতি থাকা উচিত। তাঁর মতে, শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক যন্ত্রণা অনেক গভীর। তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন যে দুঃখ-কষ্টই মানুষকে মহৎ কর্ম ও সাফল্যের পথে উৎসাহিত করে।
চিঠির শেষে দিলীপকুমার রায়ের পাঠানো বইগুলির প্রশংসা করে নেতাজি জানিয়েছেন যে, জেলের অন্যান্য বন্দিরাও সেগুলি পড়ে উপকৃত হচ্ছেন। তাই তিনি বইগুলি ফেরত পাঠাতে দেরি করছেন এবং আরও বই পাঠানোর অনুরোধ করেছেন।
ক্লাস VIII বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
(১.১) সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কেন?
উত্তর: ভারতবিদ্বেষী ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহারের অভিযোগে সুভাষচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।
(১.২) রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে তিনি কোন্ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর: রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।
২. অনধিক তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
২.১ তোমার পাঠ্য পত্রখানি কে, কোথা থেকে, কাকে লিখেছিলেন?
উত্তর: আমাদের পাঠ্য পত্রখানির লেখক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি মান্দালয় জেল থেকে তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে এই পত্রখানি লিখেছিলেন।
২.২ কোন্ ব্যাপারটিকে পত্রলেখক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেছেন?
উত্তর: কারাবাসের কষ্টকে বড়ো না করে নেতাজি বলেছেন যে এই পরিবেশ মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাতে সাহায্য করে। তাই তিনি দিলীপকুমার রায়কে কারাবাসকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।
২.৩ বন্দিদশায় মানুষের মনে শক্তি সঞ্চারিত হয় কীভাবে?
উত্তর: সুভাষচন্দ্রের মতে, বন্দিদশায় মানুষের মনে দার্শনিক ভাবশক্তি সঞ্চারিত হয়। মানুষ যদি নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মতো বিষয় খুঁজে পায়, তবে বন্দিদশাতেও তার কষ্ট কমে যায়।
২.৪ মান্দালয় জেল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: মান্দালয় জেল বার্মায়, বর্তমান মায়ানমারে অবস্থিত। ব্রিটিশরা বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সেখানে বন্দি করে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত।
২.৫ ভারতীয় জেল বিষয়ে একটি পুস্তক সুভাষচন্দ্রের লেখা হয়ে ওঠেনি কেন?
উত্তর: ভারতীয় জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র অনায়াসেই অনেক কিছু লিখতে পারতেন। কিন্তু চিঠির ক্ষুদ্র পরিসরে এত কথা লেখা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, একটি বই লেখার জন্য যে উদ্যম ও শক্তি প্রয়োজন, তা তাঁর তখন ছিল না। তাই ভারতীয় জেল বিষয়ে একটি পুস্তক তাঁর লেখা হয়ে ওঠেনি।
২.৬ সুভাষচন্দ্র কেন দিলীপ রায়ের প্রেরিত বইগুলি ফেরত পাঠাতে পারেননি?
উত্তর: মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায় দিলীপকুমার রায় সুভাষচন্দ্রকে কিছু বই পাঠিয়েছিলেন। বইগুলির গুণের প্রশংসা করে নেতাজি জানান যে এগুলি অনেক বন্দিই পড়ছেন। তাই তিনি তখনই বইগুলি ফেরত পাঠাতে পারেননি। উপরন্তু, তিনি আরও ভালো বই পাঠানোর জন্য দিলীপ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন।
৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কয়েকটি বাক্যে লেখো।
৩.১ নেতাজি ভবিষ্যতের কোন্ কর্তব্যের কথা এই চিঠিতে বলেছেন? কেন এই কর্তব্য স্থির করেছেন? কারা-শাসনপ্রণালী বিষয়ে কাদের পরিবর্তে কাদের প্রণালীকে তিনি অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেছেন?
উত্তর: মান্দালয় জেল থেকে ২ মে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রিয় বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক চিঠিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের কারা-শাসন পদ্ধতির সংস্কার ঘটানোই তাঁর ভবিষ্যতের একটি প্রধান কর্তব্য হবে।
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের কারণে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন যে কারাগারের পরিবেশে বন্দিদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যায়, বরং নৈতিক উন্নতির পরিবর্তে তারা আরও হীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যই তিনি এই কর্তব্য স্থির করেছিলেন।
তিনি আরও বলেছেন যে, ভারতীয় কারা-শাসনপ্রণালীকে ব্রিটিশ আদর্শ থেকে মুক্ত করে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের মতো উন্নত দেশের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।
৩.২ “সেজন্য খুবই খুশি হয়েছি।”—বক্তা কে? তিনি কীজন্য খুশি হয়েছেন?
উত্তর: প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটি মান্দালয় কারাগারে বন্দি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর।
তিনি খুশি হয়েছেন এই কারণে যে, রাজনৈতিক বন্দিদের কাছে সাধারণত কোনো চিঠি পৌঁছোনোর আগে তা ‘double distillation’ অর্থাৎ দু’বার পরীক্ষা করা হত। যদি কোনো আপত্তিকর বিষয় পাওয়া যেত, তবে চিঠিটি আর বন্দির হাতে পৌঁছত না। কিন্তু এবার তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের ২৪ মার্চ, ১৯২৫ তারিখের লেখা চিঠিটি কোনো বাধা ছাড়াই তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছিল। তাই তিনি খুশি হয়েছেন।
৩.৩ “আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন।”—কে, কাকে এ কথা বলেছেন? কীসের উত্তর দেবার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: উক্তিটি বলেছেন মান্দালয় কারাগারে বন্দি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি এটি বলেছেন তাঁর প্রিয়বন্ধু প্রখ্যাত সুরকার, গীতিকার ও সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায়কে।
এখানে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ তারিখে দিলীপকুমার রায়ের লেখা এক চিঠির উত্তর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন যে সেই চিঠিটি তাঁর হৃদয়কে কোমলভাবে স্পর্শ করেছে এবং তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তার উত্তর দেওয়া তাঁর কাছে কঠিন মনে হয়েছে। উপরন্তু, রাজনৈতিক বন্দির সব চিঠিই সেন্সরের (Censor) হাতে পড়ে। ফলে তাঁর আন্তরিক আবেগ ও চিন্তা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে যেত। তাই এমন চিঠির উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সুকঠিন বলে মনে হয়েছে।
৩.৪ “পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যেজন ভুক্তভোগী।”—উদ্ধৃতিটির সমার্থক বাক্য পত্রটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। সেই বাক্যটি থেকে লেখকের কোন্ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর: পাঠ্যপত্র থেকে উদ্ধৃতিটির সমার্থক বাক্যটি হল—
“আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম।”
এই বাক্যে নেতাজির সহানুভূতিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, ভুক্তভোগী না হলে অপরের দুঃখ-কষ্ট বোঝা সম্ভব নয়। নেতাজি নিজে কারাবাস ভোগ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কারাবন্দিদের প্রতি সাধারণ মানুষ প্রায়শই সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। কিন্তু কারাগারের কঠোর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। তাই তিনি লিখেছেন, যদি নিজে কারাবন্দি না হতেন, তবে তিনিও হয়তো অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতেন না। এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অপরাধী সংস্কারের বিষয়ে গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।
৩.৫ “আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।”—কোন প্রসঙ্গে বক্তার এই উক্তি? জেলজীবনে তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে কীভাবে লাভবান হবার কথা বলেছেন?
উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা মান্দালয় জেলের পত্র থেকে গৃহীত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তিনি প্রিয় বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেখানে কারাবাসের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন।
তিনি লিখেছেন, জেলের নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয়। মানুষ যখন বাহ্যিক কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন নিজের মনের ভেতরে ঢুকে সে জীবনের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে পারে। তিনিও কারাবাসকালে নিজের অতীত অভিজ্ঞতা ও জটিল সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে বহুদিনের জটিল সমস্যার সমাধান তিনি নিজের মনের ভেতরেই খুঁজে পেয়েছেন।
আগের দুর্বল বা অস্পষ্ট মতামতগুলো কারাগারের নির্জনতায় ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুসংহত হয়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করেন, এভাবে চিন্তার সুযোগ পেয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটছে। তাই তিনি মনে করেন, তাঁর কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তিনি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভবান হবেন।
ক্লাস ৮ বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
৩.৬ “Martyrdom” শব্দটির অর্থ কী? এই শব্দটি উল্লেখ করে বক্তা কী বক্তব্য রেখেছেন?
উত্তর: Martyrdom শব্দটির অর্থ হলো ‘আত্মবলিদান’ বা ‘মহৎ কারণ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য প্রবল কষ্টভোগ’।
নেতাজির বন্ধু দিলীপকুমার রায় তাঁর কারাবাসকে Martyrdom বা শহিদত্ব বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু নেতাজি বিনয়ের সঙ্গে এই অভিহিতিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, বন্ধুর এই মন্তব্য তাঁর মহৎ মানসিকতার পরিচায়ক হলেও তিনি নিজেকে শহিদ মনে করার মতো স্পর্ধা রাখেন না।
নেতাজি আরও জানিয়েছেন, তাঁর মধ্যে সামান্য কিছু রসবোধ (humour) ও মাত্রাবোধ (proportion) আছে। তাই তিনি আত্মগরিমা বা অহংকারকে প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁর মতে, Martyrdom কোনো ব্যক্তিগত গৌরব নয়, বরং তা একটি আদর্শ। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি সংগ্রামী জীবন কাটাতে চান।
এই বক্তব্যে নেতাজির আত্মসংযম, বিনয়, রসবোধ, অহংকারবর্জিত মানসিকতা এবং উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৩.৭ “যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দি করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়।”—কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? ‘তাদের মূল্য’ বিষয়ে লেখকের বক্তব্য আলোচনা করো।
উত্তর: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তারিখে মান্দালয় জেল থেকে প্রিয়বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক চিঠিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।
তিনি দীর্ঘ কারাবাসের কুফল প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, জেলের খারাপ খাবার, শরীরচর্চার অভাব, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, আনন্দ-বিনোদনের সুযোগ না পাওয়া—এসব কারণে মানুষ অকালেই দেহে ও মনে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। নেতাজি লোকমান্য তিলকের অকালমৃত্যুর জন্য তাঁর মান্দালয়ের ছ’বছরের কঠোর বন্দিজীবনকেই দায়ী করেছেন।
নেতাজি আরও বলেন, সাধারণ জীবনে আমরা প্রায়শই পিকনিক, বন্ধুদের সঙ্গে নিরালায় আলাপচারিতা, গান-বাজনা, খোলা জায়গায় খেলা, কিংবা সাহিত্যচর্চার মতো বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিই না। কিন্তু যখন আমাদের এসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে জোর করে বন্দি করে রাখা হয়, তখনই এগুলোর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায়।
তাঁর মতে, যদি কারা-শাসনপ্রণালীতে মৌলিক সংস্কার আনা না হয়, তবে বন্দিদের নৈতিক উন্নতি হবে না, বরং তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে নেতাজি আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাধারণ বন্দিদের জীবনে আনন্দ, সৃজনশীলতা ও মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।
৩.৮ “মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়।”—যে ঘটনায় লেখকের মনে এই উপলব্ধি ঘটে তার পরিচয় দাও।
উত্তর: মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তারিখে লেখা পত্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।
তিনি লিখেছেন, ভারতীয় কারাগারে বন্দিদের দৈহিক কষ্ট যেমন আছে, তার চেয়েও বেশি রয়েছে মানসিক যন্ত্রণা। যেসব বন্দি নিয়মিত শারীরিক আঘাত বা অপমান সহ্য করে, তাদের মনে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়া জন্মায়। এর ফলে কারা-শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাদের নৈতিক সংশোধন ঘটে না; বরং মানসিক বিকৃতি তৈরি হয় এবং তারা আরও অবনতির দিকে চলে যায়।
তবে দার্শনিক দৃষ্টিতে নেতাজি একটি ইতিবাচক দিকও দেখেছেন। জেলের একঘেয়ে, নিরানন্দময় জীবন মানুষকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়, জীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার অবসর দেয়। এর ফলে আত্মউন্নতি সম্ভব হয়।
কিন্তু নেতাজি মনে করেন, বর্তমান ব্রিটিশ কারা-শাসনপ্রণালীর মূল লক্ষ্য বন্দিদের সবসময় এই অনুভূতিতে আচ্ছন্ন রাখা যে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কঠোর ও নিরানন্দময়। তাই শারীরিক কষ্টের থেকেও মানসিক নির্যাতন এখানে বেশি প্রখর। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে আলোচ্য মন্তব্য লিখতে বাধ্য করেছে।
৩.৯ এই চিঠিতে কারাবন্দি অবস্থাতেও দুঃখকাতর, হতাশাগ্রস্ত নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী নেতাজির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।—পত্র অবলম্বনে নিজের ভাষায় মন্তব্যটির যাথার্থ্য পরিস্ফুট করো।
উত্তর: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে মান্দালয় জেল থেকে প্রিয়বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিটি নেতাজির এক আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। সাধারণত দীর্ঘ কারাবাসের দুঃসহ অভিজ্ঞতা মানুষকে ভেঙে দেয়, কিন্তু নেতাজি সেখানে থেকেও দুঃখকাতর বা হতাশ হননি। বরং তিনি ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করেছেন।
চিঠিতে তিনি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় কারা-শাসনপ্রণালীর কুৎসিত রূপের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে এর আমূল সংস্কার করাই হবে তাঁর অন্যতম ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। তিনি সমাজে অপরাধী ও বন্দিদের প্রতি সহানুভূতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।
বন্ধুর পাঠানো বই পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং সেই বইগুলি তিনি জেলের অন্য বন্দিদের হাতেও তুলে দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি কষ্টের মাঝেও নিজেকে ও অন্যদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।
তাঁর বিশ্বাস—“আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।” এই দার্শনিক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নেতাজি দুঃখকষ্টকে বাধা হিসেবে নয়, বরং শক্তি ও প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, বিনা দুঃখকষ্টে পাওয়া জিনিসের মূল্য নেই; বরং কষ্ট সহ্য করেই বড় অর্জন সম্ভব।
সব মিলিয়ে বলা যায়, এই চিঠিতে নেতাজি কেবল এক বন্দি নন, বরং একজন আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী, কর্মপন্থী এবং দৃঢ়চেতা বিপ্লবী।
৩.১০ কারাগারে বসে নেতাজির যে ভাবনা, যে অনুভব, তার অনেকখানি কেন অকথিত রাখতে হবে?
উত্তর: মান্দালয় কারাগার থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মে তারিখে দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে নেতাজি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, কারাবন্দি অবস্থায় তাঁর অনেক ভাবনা ও অনুভব অকথিত রাখতে হবে।
এর প্রধান কারণ দু’টি—
১. ভাষার সীমাবদ্ধতা ও গভীর আবেগ: বন্ধু রায়ের চিঠি তাঁর মনে যে গভীর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, তা ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা তাঁর কাছে কঠিন মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, কিছু আবেগ এত গভীর হয় যে কাগজে কলমে তা ধরা যায় না।
২. ‘Censor’-এর ভয়: কারাগারে বন্দিদের চিঠি সেন্সরের হাতে পড়ে। সেখানে যদি কোনো বক্তব্য আপত্তিকর বলে মনে হয়, তবে তা পৌঁছাতেই দেওয়া হয় না। ফলে নেতাজি মনে করেন, তাঁর অন্তরের অনেক ভাবনা অকালে প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে, যা তিনি চান না।
তাই নেতাজি বলেছেন, যতদিন তিনি কারাগারে থাকবেন, তাঁর মনের অনেকখানি অংশ অকথিতই থেকে যাবে। মুক্ত জীবনেই তিনি সেসব মুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
৪. নীচের বাক্যগুলির তথ্যগত অশুদ্ধি সংশোধন করো।
৪.১ নেতাজি মনে করতেন না যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।
উত্তর: নেতাজি মনে করতেন যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।
৪.২ কারাগারে বন্দি অবস্থায় নেতাজি সুভাষ গীতার আলোচনা লিখেছিলেন।
উত্তর: কারাগারে বন্দি অবস্থায় লোকমান্য তিলক গীতার আলোচনা লিখেছিলেন।
৪.৩ জেলজীবনের কষ্ট মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বলে নেতাজি মনে করতেন।
উত্তর: জেলজীবনের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে নেতাজি মনে করতেন।
অষ্টম শ্রেণী বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
৫. নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাসবদ্ধ পদ বেছে নিয়ে ব্যাসবাক্য-সহ সমাসের নাম লেখো।
৫.১ তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে কোমলভাবে স্পর্শ করেছে।
উত্তর: হৃদয়তন্ত্রী – হৃদয়ের তন্ত্রী – কর্মধারয় সমাস।
৫.২ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি।
উত্তর: অজ্ঞাত – যা জানা যায়নি – না-তৎপুরুষ সমাস।
৫.৩ তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে।
উত্তর: নিঃসংশয় – যে সংশয় নেই – না-বহুব্রীহি সমাস।
৫.৪ নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।
উত্তর: দণ্ডবিধি – দণ্ডের বিধি – নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস।
৫.৫ লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার আলোচনা লেখেন।
উত্তর: লোকমান্য – যে লোক দ্বারা মান্য – তৎপুরুষ সমাস।
৬. শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো
পাঠক – √পাঠ্ (পড়) + ক = যে পাঠ করে
দর্শন – √দৃশ্ (দেখা) + অন্ = দেখা বা জ্ঞান
দৈহিক – দেহ + ইক = দেহসংক্রান্ত
আধ্যাত্মিক – অধ্যাত্ম (আত্মা) + ইক = আত্মাসংক্রান্ত
ভণ্ডামি – ভণ্ড + আমি (প্রত্যয়) = ভণ্ডের স্বভাব বা ভণ্ডের কাজ
সমৃদ্ধ – সম্ + √ঋধ্ (বৃদ্ধি) + ক্ত = সম্যক্ বৃদ্ধি পাওয়া
মহত্ত্ব – মহৎ + ত্ব = মহৎ হওয়ার গুণ
অভিজ্ঞতা – অভি + √জ্ঞা (জানা) + ত = জানা থেকে অভিজ্ঞতা
৭. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন করো
৭.১ আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন।
না-সূচক বাক্যে: আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়।
৭.২ সেইজন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়।
প্রশ্নবোধক বাক্যে: সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায় না কি?
৭.৩ লজ্জায় তারা বাড়িতে কোনো সংবাদ দেয়নি।
যৌগিক বাক্যে: তারা লজ্জা পেয়েছিল, তাই বাড়িতে কোনো সংবাদ দেয়নি।
৭.৪ কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে।
সরল বাক্যে: মানুষ ভিতর থেকে কতকগুলি অভাব পূর্ণ করে তুলতে পারে।
৭.৫ বিনা দুঃখকষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্য আছে?
নির্দেশক বাক্যে: দুঃখকষ্টে যা লাভ করা যায়, তারই মূল্য আছে।
ক্লাস VIII বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
৮. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।
৮.১ “শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, সংশোধনই হওয়া উচিত জেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য।”- তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর: আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কারাগারের উদ্দেশ্য যদি কেবল কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তবে বন্দির মানসিক বিকৃতি ও অবক্ষয়ই ঘটে। কিন্তু সংশোধনের সুযোগ পেলে বন্দি নতুনভাবে জীবন গড়তে পারে। আজও পৃথিবীর বহু দেশে জেলকে বলা হয় “সংশোধনাগার”। সেখানে কয়েদিরা পড়াশোনা, সংগীত, নাটক, চিত্রকলা, খেলাধুলো ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে যুক্ত হয়। এর ফলে তাদের ভেতরের হিংসা ও অপরাধবোধ কমে আসে এবং জীবনে নতুন আশা জন্মায়। পাঠ্যাংশেও নেতাজি আলিপুর জেলের সংগীতচর্চার উদাহরণ টেনে বলেছেন যে এ ধরনের আয়োজন কয়েদির মানসিক উন্নতিতে সহায়ক। শুধু কঠোর শাস্তি মানুষকে সংশোধন করে না, বরং তার মনোবল ভেঙে দেয়। তাই জেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষকে সৎ ও উন্নত জীবনের পথে ফেরানো।
৮.২ “আমাদের দেশের আর্টিস্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো।”- এ প্রসঙ্গে কারাজীবন যাপন করা কয়েকজন সাহিত্যিকের নাম এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করো।
উত্তর: নেতাজি এই বক্তব্যে কারাজীবনের অভিজ্ঞতার প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। কারাবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই নজরুল রচনা করেছেন সর্বহারা, বিষের বাঁশী, ছায়ানট, ফণীমনসা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, যেখানে তাঁর বিপ্লবী চেতনা ও বিদ্রোহী মানস প্রকাশ পেয়েছে।
এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন লেখকের রচনায় কারাবাসের অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাষাণপুরী, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, অতীন্দ্রনাথ বসুর বি কেলাস—সবই কারাজীবন-প্রসূত সাহিত্যকীর্তি। এসব রচনা প্রমাণ করে যে কারাবাস শুধু দুঃখের অভিজ্ঞতা নয়, সাহিত্য-শিল্পকে সমৃদ্ধ করার এক গভীর অনুপ্রেরণাও হতে পারে।
৮.৩ পত্রটি পড়ে কারাজীবন বিষয়ে তোমার যে ধারণা ও অনুভূতি জন্মেছে তা জানিয়ে বস্তুকে একটি পত্র লেখো।
উত্তর:
প্রিয় অনিরুদ্ধ,
আজ বাংলা পাঠ্যবই সাহিত্যমেলা-য় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মান্দালয় জেল থেকে দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠি পড়লাম। পড়তে গিয়ে গভীরভাবে অনুভব করলাম কারাজীবনের কঠোরতা, কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা।
জেলে বন্দিদের শুধু শরীর নয়, মনকেও কীভাবে আঘাত করা হতো, কীভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের রাখা হতো—তা নেতাজি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তবে এত দুঃখ-যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি কখনও হতাশ হননি; বরং ভবিষ্যতে কারা-শাসনপ্রণালীর সংস্কারের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর লেখা পড়ে বুঝলাম, জেলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অপরাধীর সংশোধন, নিছক শাস্তি দেওয়া নয়।
চিঠিটি পড়ার পর আমার মনে বন্দিদের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। পাশাপাশি বুঝেছি—দুঃখকষ্টও মানুষকে মহান উদ্দেশ্যের পথে দৃঢ় করে তোলে। সুযোগ পেলে তুই-ও একবার তরুণের স্বপ্ন বইটি পড়বি। এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকিস।
তোর বন্ধু
………
৮.৪ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বস্তুর সম্পর্কে আরও জেনে ‘সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।
উত্তর:
সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওডিশার কটকে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবনেই তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনকে অপদস্থ করার ঘটনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেও তিনি দমে যাননি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং পরে আইসিএস পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের অধীনে চাকরি করা তাঁর বিবেকসম্মত মনে হয়নি; তাই তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করেন।
প্রথমে গান্ধিজি, পরে চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। মান্দালয় জেলে কঠোর কারাবাসও তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্নকে দমাতে পারেনি। ১৯৪১ সালে তিনি গৃহবন্দিত্ব ভেঙে পালিয়ে বিদেশে যান। জার্মানি, ইতালি ও জাপানে গিয়ে তিনি ভারতমুক্তির কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালান। পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নানা ধর্ম ও ভাষার মানুষকে একত্রিত করে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।
১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলেও দেশবাসী আজও সেই মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি।
স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার মহত্ত্বে সুভাষচন্দ্র আজও অমর। তাঁর অদম্য দেশপ্রেম আমাদের চিরকাল অনুপ্রেরণা জোগাবে।
অষ্টম শ্রেণী বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) MCQ প্রশ্ন উত্তর
(1) “জেলখানার চিঠি” কার লেখা?
(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(b) সুভাষচন্দ্র বসু
(c) মহাত্মা গান্ধী
(d) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
Answer: (b) সুভাষচন্দ্র বসু
(2) এই চিঠিটি কোথা থেকে লেখা হয়েছিল?
(a) আলিপুর জেল
(b) আন্দামান জেল
(c) মান্দালয় জেল
(d) প্রেসিডেন্সি জেল
Answer: (c) মান্দালয় জেল
(3) চিঠির তারিখ কত?
(a) ২।৫।১৯২৩
(b) ২৪।৩।১৯২৫
(c) ২।৫।১৯২৫
(d) ২৫।৫।১৯২৪
Answer: (c) ২।৫।১৯২৫
(4) চিঠিটি কাকে লেখা হয়েছিল?
(a) দিলীপকে
(b) রণেনকে
(c) সুভ্রকে
(d) বিমলকে
Answer: (a) দিলীপকে
(5) সুভাষচন্দ্র কারাবাসকে কিভাবে দেখেছিলেন?
(a) দুঃখজনক
(b) আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুযোগ
(c) খেলাধুলার মতো
(d) সহজ ব্যাপার
Answer: (b) আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুযোগ
(6) কারা-সংস্কার বিষয়ে তিনি কোন দেশের দৃষ্টান্ত দিলেন?
(a) জাপান
(b) আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস
(c) ফ্রান্স
(d) ইংল্যান্ড
Answer: (b) আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস
(7) দীর্ঘ কারাবাসে মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিপদ কী?
(a) দুর্বলতা
(b) অকাল বার্ধক্য
(c) অসুস্থতা
(d) ক্ষুধা
Answer: (b) অকাল বার্ধক্য
(8) লোকমান্য তিলক কারাগারে কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন?
(a) গীতার আলোচনা
(b) আনন্দমঠ
(c) ভারতের স্বাধীনতা
(d) বন্দেমাতরম্
Answer: (a) গীতার আলোচনা
(9) কার কবিতায় জেল-অভিজ্ঞতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলে সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন?
(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(b) কাজী নজরুল ইসলাম
(c) জীবনানন্দ দাশ
(d) বঙ্কিমচন্দ্র
Answer: (b) কাজী নজরুল ইসলাম
(10) জেলের পরিবেশ মানুষকে কেমন করে তোলে?
(a) জ্ঞানী করে
(b) বিকৃত অমানুষ করে
(c) সুস্থ করে
(d) সদয় করে
Answer: (b) বিকৃত অমানুষ করে
(11) কারাবন্দীদের কীভাবে দেখা উচিত বলে লেখক মনে করেন?
(a) অপরাধী হিসাবে
(b) মানসিক রোগী হিসাবে
(c) শত্রু হিসাবে
(d) সমাজচ্যুত হিসাবে
Answer: (b) মানসিক রোগী হিসাবে
(12) সুভাষচন্দ্রের মতে কারাবাস কাকে বেশি কষ্ট দেয়?
(a) শারীরিকভাবে
(b) মানসিকভাবে
(c) অর্থনৈতিকভাবে
(d) রাজনৈতিকভাবে
Answer: (b) মানসিকভাবে
(13) আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য কী ব্যবস্থা ছিল?
(a) নাটক
(b) সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত
(c) খেলাধুলা
(d) বক্তৃতা
Answer: (b) সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত
(14) রাজনৈতিক অপরাধীদের সান্ত্বনা কী?
(a) মুক্তির পর সমাজ তাদের বরণ করে নেয়
(b) তারা অর্থ পায়
(c) তারা বিদেশে যায়
(d) তারা আর জেলে যায় না
Answer: (a) মুক্তির পর সমাজ তাদের বরণ করে নেয়
(15) সাধারণ অপরাধীরা কিসের কারণে সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়?
(a) টাকা নেই বলে
(b) তাদের পরিবার জানে না বলে
(c) কেউ তাদের মানে না বলে
(d) কাজ হারায় বলে
Answer: (b) তাদের পরিবার জানে না বলে
(16) চিঠিতে সুভাষচন্দ্র কোন মহৎ অনুভূতির কথা বলেছেন?
(a) হাসি
(b) সহানুভূতি
(c) ভয়
(d) প্রতিশোধ
Answer: (b) সহানুভূতি
(17) সুভাষচন্দ্রের মতে বন্দিদশা মানুষকে কী করার সুযোগ দেয়?
(a) ঘুমানো
(b) জীবনের চরম সমস্যাগুলি বোঝা
(c) রাজনীতি করা
(d) লেখাপড়া না করা
Answer: (b) জীবনের চরম সমস্যাগুলি বোঝা
(18) তিনি নিজের কারাবাসকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
(a) Martyrdom (শহীদত্ব)
(b) স্বাধীনতা
(c) আনন্দ
(d) পরীক্ষা
Answer: (a) Martyrdom (শহীদত্ব)
(19) সুভাষচন্দ্রের মতে কোন জিনিসগুলো বন্দিদের জীবন সরস করে তোলে?
(a) টাকা
(b) পিকনিক, সংগীত, সাহিত্যচর্চা
(c) চাকরি
(d) সোনা
Answer: (b) পিকনিক, সংগীত, সাহিত্যচর্চা
(20) কারাবাস থেকে তিনি ভবিষ্যতের জন্য কী শিখেছেন?
(a) কারা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
(b) রাজনীতি শেখা
(c) গান শেখা
(d) ব্যবসা করা
Answer: (a) কারা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
অষ্টম শ্রেণী বাংলা
জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) SAQ প্রশ্ন উত্তর
১. দিলীপকুমার রায়ের প্রতি সুভাষচন্দ্রের অনুভূতি কতটা গভীর তা এই পাঠাংশ অবলম্বনে উল্লেখ করো।
উত্তর: বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও লেখক দিলীপকুমার রায় ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায়ও তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। দিলীপকুমার রায় তাঁকে বই পাঠিয়ে মানসিক অবলম্বন জুগিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন—“তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন।” এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, দিলীপকুমার রায়ের প্রতি সুভাষচন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অনুভূতি কতটা আন্তরিক ও গভীর ছিল।
২. জেলে থাকার ইতিবাচক দিক হিসেবে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য কী?
উত্তর: সুভাষচন্দ্র বসুর মতে, জেলে বন্দি অবস্থায় মানুষের মধ্যে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। বন্দি মানুষ নিজের জীবন নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়, আত্মবিশ্লেষণ করে এবং মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। ফলে কারাবাসের মধ্য দিয়ে অনেক সময় অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে।
৩. বন্দি মানুষের উপর জেলখানার পরিবেশ কীরূপ প্রভাব ফেলে?
অথবা, “মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কী কঠোর ও নিরানন্দময়”—যে ঘটনায় লেখকের মনে এই উপলব্ধি ঘটে তার পরিচয় দাও।
উত্তর: সুভাষচন্দ্র বসুর মতে, জেলখানার পরিবেশ অস্বাভাবিক ও নিরানন্দময়। সেখানে মুক্তজীবনের মতো স্বাধীনতা নেই। কারা প্রশাসনের কঠোর নিয়মকানুন ও আচরণ বন্দিদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে জেলের পরিবেশ মানুষকে স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুত করে অনেক সময় অমানুষ করে তোলার মতো প্রভাব ফেলে।
৪. জেলখানায় রাজনৈতিক ও সাধারণ বন্দিদের মধ্যে লেখক কী পার্থক্য লক্ষ করেছেন?
উত্তর: সুভাষচন্দ্রের মতে, রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি সমাজের সহানুভূতি থাকে। তারা মুক্তি পাওয়ার পর সমাজে সম্মান পায়। কিন্তু সাধারণ বন্দিরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মুক্তির পরও সাধারণ বন্দি অনেক সময় সমাজের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতেই লজ্জা বোধ করে। ফলে তারা মানসিকভাবে আরও ভেঙে পড়ে।
৫. দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে মানুষের অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়ার পিছনে কারণ কী?
উত্তর: সুভাষচন্দ্রের মতে, দীর্ঘদিন বন্দি থাকার ফলে খারাপ খাদ্য, ব্যায়ামের অভাব, আনন্দহীনতা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, অধীনতার শৃঙ্খল, বন্ধুজনের অনুপস্থিতি ইত্যাদির কারণে মানুষের অকালবার্ধক্য নেমে আসে।
৬. লোকমান্য তিলক সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু ‘জেলখানার চিঠি’-তে কী ধারণা পোষণ করেন?
উত্তর: সুভাষচন্দ্র বসু লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মতে, দীর্ঘ কারাবাসে তিলকের দেহ ভেঙে গেলেও তাঁর মানসিক শক্তি অটুট ছিল। তিলকের লেখা গীতার কর্মযোগ ব্যাখ্যা তাঁর অমিত মানসিক শক্তির প্রমাণ। তবে মান্দালয়ে ছয় বছরের কঠোর বন্দিদশা তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।
৭. “ব্যাপারটিকে তুমি একটা ‘martyrdom’ বলে অভিহিত করেছ”—উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন ব্যাপারটিকে ‘martyrdom’ বলেছেন?
উত্তর: ‘জেলখানার চিঠি’-তে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন যে, বন্ধু দিলীপকুমার রায় তাঁর কারাবাসকেই ‘martyrdom’ বা আত্মবলিদান বলেছেন। তবে সুভাষচন্দ্র নিজেকে কখনও শহিদ বা আত্মবলিদানকারী বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, এটি তাঁর কর্তব্য ও সংগ্রামের অংশমাত্র।
৮. “আমার মনে হয় অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না”—এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য কী?
উত্তর: সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, কারাবাস অপরাধীদের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে না; বরং তারা আরও অধঃপতিত হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁর মতে, অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি ও নতুন মনোভাব নিয়ে কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তর করা উচিত। এজন্য তিনি আমেরিকার উন্নত কারা-ব্যবস্থাকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন।
অষ্টম শ্রেণী বাংলা / জেলখানার চিঠি (সুভাষচন্দ্র বসু) হাতেকলমে প্রশ্ন উত্তর
আরও দেখো:
ঘুরে দাঁড়াও কবিতার প্রশ্ন উত্তর
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের প্রশ্ন উত্তর
WBNMMSE Scholarship Portal: Official Website
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল: TextbookPlus
টেলিগ্রাম গ্রুপ: GhoshClass
Facebook Group: TextbookPlus