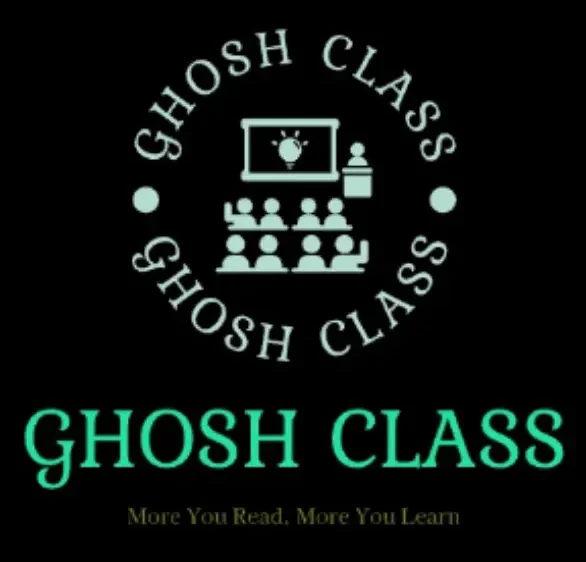এখানে মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় প্রশ্ন উত্তর শেয়ার করা হলো। / দশম শ্রেণী ইতিহাস ৭ অধ্যায় / বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় MCQ প্রশ্ন উত্তর
বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল- (মাধ্য: 2017)
ক) ১৯০৪ খ্রিঃ
খ) ১৯০৬ খ্রিঃ
গ) ১৯০৫ খ্রিঃ
ঘ) ১৯১১ খ্রিঃ
উত্তর: গ) ১৯০৫ খ্রিঃ
২. মাতঙ্গিনী হাজরা ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে স্থানে- (মাধ্য: 2017)
ক) সুতাহাটা
খ) বরিশাল
গ) পুরুলিয়া
ঘ) তমলুক
উত্তর: ঘ) তমলুক
৩. দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- (মাধ্য: 2018)
ক) কল্পনা দত্ত
খ) বাসন্তী দেবী
গ) উর্মিলা দেবী
ঘ) লীলা নাগ (রায়)
উত্তর: ঘ) লীলা নাগ (রায়)
৪. নারী কর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- (মাধ্য: 2018)
ক) কল্পনা দত্ত
খ) বাসন্তী দেবী
গ) উর্মিলা দেবী
ঘ) লীলা রায় (নাগ)
উত্তর: খ) বাসন্তী দেবী
৫. সূর্যসেন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলটির নাম ছিল- (মাধ্য: 2017)
ক) অনুশীলন সমিতি
খ) বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স
গ) সদর দল
ঘ) ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি
উত্তর: ঘ) ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি
৬. দলিতদের ‘হরিজন’ আখ্যা দিয়েছিলেন- (মাধ্য: 2018)
ক) জ্যোতিবা ফুলে
খ) নারায়ণ গুরু
গ) গান্ধিজি
ঘ) ডঃ আম্বেদকর
উত্তর: গ) গান্ধিজি
৭. বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন- (মাধ্য: 2019)
ক) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
খ) সুনীতি চৌধুরি
গ) কল্পনা দত্ত
ঘ) বীণা দাস
উত্তর: ঘ) বীণা দাস
৮. অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন- (মাধ্য: 2019)
ক) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু
খ) কৃষ্ণকুমার মিত্র
গ) চিত্তরঞ্জন দাস
ঘ) আনন্দমোহন বসু
উত্তর: খ) কৃষ্ণকুমার মিত্র
৯. ভাইকম সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল- (মাধ্য: 2019)
ক) মালাবারে
খ) মহারাষ্ট্রে
গ) মাদ্রাজে
ঘ) গোদাবরী উপত্যকায়
উত্তর: ক) মালাবারে
১০. মাদ্রাজে আত্মসম্মান আন্দোলন শুরু করেন- (মাধ্য: 2020)
ক) রামস্বামী নাইকার
খ) নারায়ণ গুরু
গ) ভীমরাও আম্বেদকর
ঘ) গান্ধিজি
উত্তর: ক) রামস্বামী নাইকার (পেরিয়ার)
মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় স্তম্ভ মেলানো প্রশ্ন উত্তর
বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
২. ক স্তম্ভের সাথে খ স্তম্ভ মেলাও:
| ক-স্তম্ভ | খ-স্তম্ভ |
|---|---|
| ১. ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ | (ক) সরলাদেবী চৌধুরাণী |
| ২. ১৬ অক্টোবর | (খ) ঊর্মিলা দেবী |
| ৩. ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ | (গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী |
| ৪. ৪২-এর আন্দোলন | (ঘ) আশালতা সেন |
| ৫. ‘গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি’ | (ঙ) লীলা নাগ |
| ৬. স্ট্যানলি জ্যাকসন | (চ) রাখিবন্ধন |
| ৭. ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ | (ছ) কনকলতা বড়ুয়া |
| ৮. ‘দীপালি সংঘ’ | (জ) বীণা দাস |
| ৯. ‘গুলামগিরি’ | (ঝ) প্রমথরঞ্জন ঠাকুর |
| ১০. কেরল | (ঞ) নারায়ণ গুরু |
| ১১. সত্যশোধক সমাজ | (ট) জ্যোতিরাও ফুলে |
| ১২. জাস্টিস পার্টি | (ঠ) মাদ্রাজ |
| ১৩. রামস্বামী নায়কার | (ড) আত্মমর্যাদা আন্দোলন |
| ১৪. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা | (ঢ) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ |
| ১৫. নমঃশূদ্র আন্দোলন | (ণ) সরলাদেবী চৌধুরাণী |
| ১৬. নওজোয়ান ভারতসভা | (ত) ভগৎ সিং |
উত্তর:
১. ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
২. ১৬ অক্টোবর — রাখিবন্ধন
৩. ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ — আশালতা সেন
৪. ৪২-এর আন্দোলন — কনকলতা বড়ুয়া
৫. ‘গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি’ — ঊর্মিলা দেবী
৬. স্ট্যানলি জ্যাকসন — বীণা দাস
৭. ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ — সরলাদেবী চৌধুরাণী
৮. ‘দীপালি সংঘ’ — লীলা নাগ
৯. ‘গুলামগিরি’ — জ্যোতিরাও ফুলে
১০. কেরল — নারায়ণ গুরু
১১. সত্যশোধক সমাজ — ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ
১২. জাস্টিস পার্টি — মাদ্রাজে
১৩. রামস্বামী নায়কার — আত্মমর্যাদা আন্দোলন
১৪. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা — ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
১৫. নমঃশূদ্র আন্দোলন — প্রমথরঞ্জন ঠাকুর
১৬. নওজোয়ান ভারতসভা — ভগৎ সিং
মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর
বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
১. মাস্টারদা নামে কে পরিচিত ছিলেন? (মাধ্যঃ -17)
উত্তর: সূর্য সেন।
২. মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে? (মাধ্য: -18)
উত্তর: শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর।
৩. ‘গান্ধিবুড়ি’ কাকে বলা হত?
উত্তর: মাতঙ্গিনী হাজরা।
৪. ঊষা মেহতা কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
৫. পুণা চুক্তি (১৯৩২) কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? (মাধ্য: -19, 20)
উত্তর: মহাত্মা গান্ধি ও বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে।
৬. “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে” (করেশে ইয়া মরেঙ্গে)-এর ডাক কে দিয়েছিলেন?
উত্তর: মহাত্মা গান্ধি।
৭. কোন বিদেশিনি ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন?
উত্তর: ভগিনী নিবেদিতা।
৮. ভগিনী নিবেদিতা অনুশীলন সমিতিকে কী উপহার দিয়েছিলেন?
উত্তর: ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড।
৯. ‘দ্য স্পার্ক অফ রেভোলিউশন’ (The Spark of Revolution) গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর: অরুণচন্দ্র গুহ।
১০. বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রীরূপে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মহীয়সী নারীর নাম লেখো।
উত্তর: সৌদামিনী দেবী, সরোজিনী দেবী, দুকড়িবালা দেবী।
১১. ‘দীপালি সংঘ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: লীলা নাগ (রায়)।
১২. ‘দীপালি সংঘ’ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ঢাকায়।
১৩. ‘দীপালি সংঘ’-এর উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করা।
১৪. কোন কলেজ থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন?
উত্তর: বেথুন কলেজ।
১৫. প্রীতিলতা কোন কোন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: ঢাকার ‘দীপালি সংঘ’ ও কলকাতার ‘ছাত্রীসংঘ’।
১৬. ‘ফুলতার’ কার ছদ্মনাম?
উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর।
১৭. ভারতের প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহিদ কে?
উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
১৮. এশিয়ার প্রথম নারীবাহিনীর নাম কী?
উত্তর: ঝাঁসির রানি রেজিমেন্ট।
১৯. ‘ঝাঁসির রানি রেজিমেন্ট’ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে।
২০. ‘ঝাঁসির রানি রেজিমেন্ট’-এর প্রধান দায়িত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন।
২১. ‘অনুশীলন সমিতি’ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ঢাকায়।
মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর
বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
১. কে ছাত্রদের ‘স্বদেশি আন্দোলনের’ ‘স্বনিয়োজিত প্রচারক’ বলে অভিহিত করে? এমন বলার কারণ কী?
উত্তর: স্বদেশি যুগের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ছাত্রদের ‘স্বদেশি আন্দোলনের স্বনিয়োজিত প্রচারক’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, ছাত্ররা কোনো সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বদেশি প্রচারে এগিয়ে আসে। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বদেশি শিল্পের ব্যবহার প্রচার করত, বিদেশি পণ্যের বয়কট করত এবং আন্দোলনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত।
২. রশিদ আলি দিবস কেন পালিত হয়েছিল?
উত্তর: ১৯৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ক্যাপ্টেন রশিদ আলি-র বিচারে তাঁকে দণ্ডিত করা হলে বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। এই দিনে কলকাতায় ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন হয়, যেখানে পুলিশের গুলিতে বহু ছাত্র শহীদ হন।
৩. দলিত কাদের বলা হয়?
উত্তর: হিন্দু সমাজের সেই নিম্নবর্ণের মানুষদের ‘দলিত’ বলা হয়, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা, সম্পত্তি, মন্দিরপ্রবেশ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও শোষণের শিকার ছিল।
৪. অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার এক কার্লিকুলার (circular) জারি করে, যাতে ছাত্ররা যদি রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকে, তবে তাদের স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই দমননীতির প্রতিবাদে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
৫. দীপালি সঙ্ঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী বাংলার নারীদের জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন।
৬. মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয় কেন?
উত্তর: মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৬৯–১৯৪২) ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বীরাঙ্গনা।
(i) তিনি ‘গান্ধীবুড়ি’ নামে পরিচিত ছিলেন এবং ১৯৪২ খ্রিঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ‘ভগিনী সেনা’র নেতৃত্বে তমলুক থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দেন।
(ii) ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২-এ পুলিশের গুলিতে তিনি শহিদ হন।
(iii) মৃত্যুর সময়ও তিনি জাতীয় পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি এবং ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।
(iv) তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বাধীনতার পরে কলকাতার হাজরা রোড তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।
৭. অরন্ধন দিবস কী?
উত্তর: ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলার মানুষ অরন্ধন দিবস পালন করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে সেদিন সারা বাংলায় কোনো উনুন জ্বলেনি, কেউ রান্না করেননি। নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই অরন্ধন বাংলার ঐক্য ও প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।
৮. ননীবালা দেবী স্মরণীয় কেন?
উত্তর: বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবীদের সহায়তা ও সাহসিকতার জন্য ননীবালা দেবী ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তিনি একজন সাহসী নারী ছিলেন, যিনি স্বদেশের জন্য নিজের নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করেছিলেন।
(i) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় ও অস্ত্র সরবরাহ করতেন।
(ii) গ্রেফতার হয়ে জেলে অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করেননি।
(iii) বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় ও সহযোগিতা দিয়ে তাদের সাহসী করতেন।
(iv) তিনি বাংলার প্রথম মহিলা রাজবন্দি, যা নারীর সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক।
মাধ্যমিক ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর
বিংশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন
১. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল? তাদের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কি?
উত্তর: ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে সারা বাংলায় প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।
নারী সমাজের অংশগ্রহণ
১. রাখীবন্ধন ও অরন্ধন:
১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব জাগ্রত করতে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। নারী সমাজ উৎসাহভরে এতে অংশ নেয়। একই দিনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে অরন্ধন দিবস পালিত হয়, তাতেও নারীরা সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়।
২. বিদেশি দ্রব্য বর্জন:
নারীরা বিদেশি শাড়ি, চুড়ি, লবণ, মসলা, ওষুধ ইত্যাদির ব্যবহার বর্জন করে এবং বিদেশি পণ্যাগারের সামনে পিকেটিংয়ে অংশ নেয়।
৩. স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও প্রচার:
স্বর্ণকুমারী দেবী ‘সখী সমিতি’ এবং সরলাদেবী চৌধুরানী ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচার করত। ‘ভারতী’, ‘ভারত মহিলা’ প্রভৃতি পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচারে সহায়ক ভূমিকা নেয়।
৪. আন্দোলনের নেতৃত্ব:
সরলাদেবী চৌধুরানী, কুমুদিনী বসু, সুবালা আচার্য, হেমাঙ্গিনী দাস প্রমুখ নারীরা সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেন। কলকাতার বাইরে গিরিজা সুন্দরী, সরোজিনী দেবী, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, ব্রহ্মময়ী সেন প্রমুখ অংশ নেন।
৫. জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি:
নারীরা বীরাষ্টমী ব্রত, মহিলা পরিষদ, ভারত মহিলা পরিষদ, সেবা সদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটায়।
সীমাবদ্ধতা
১. উচ্চবর্ণ ও শহুরে নারীর প্রাধান্য:
অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন শহুরে উচ্চবর্ণের হিন্দু নারী। গ্রামীণ নারী ও মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।
২. সীমিত অংশগ্রহণ:
নারী সমাজের একটি ছোট অংশই সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত হয়।
৩. পুরুষ প্রাধান্য:
নারীরা আন্দোলনে অংশ নিলেও আন্দোলনের নীতি ও নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই ছিল। স্বাধীনভাবে নারীরা আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেনি।
২. দীপালী সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: দীপালী সংঘ ১৯২৩ সালে লীলা নাগ (রায়)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল —
(i) নারীদের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
(ii) শিল্পচর্চা ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।
(iii) গৃহকোণে আবদ্ধ নারী সমাজে আনন্দ, সাংস্কৃতিক বিনোদন ও নতুন জীবনের স্বাদ পৌঁছে দেওয়া।
(iv) নারীদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা।
(v) নারীদের সশস্ত্র আন্দোলনের উপযুক্ত যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা।
৩. গুরুচাঁদ ঠাকুর স্মরণীয় কেন?
উত্তর: গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬–১৯৩৭ খ্রি.) ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য উত্তরসূরী, বাঙালি সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী। তিনি দলিত ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।
(i) তাঁর উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে খুলনার দত্তডাঙ্গায় প্রথম নমঃশূদ্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
(ii) তিনি চণ্ডাল জাতিকে নমঃশূদ্র জাতিতে উত্তরণ ঘটানোর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
(iii) তিনি দলিত সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল—
“খাও বা না খাও তাতে কোন দুঃখ নাই, ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।”
তাঁর প্রচেষ্টায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।
৫. দলিত আন্দোলন বিষয়ে গান্ধী-আম্বেদকর বিতর্ক আলোচনা করো।
উত্তর: ‘দলিত’ শব্দটি এসেছে ‘দলন’ থেকে, যার অর্থ দমনকৃত বা নিপীড়িত। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে তাদের ‘তপশিলি জাতি’ ও ‘তপশিলি উপজাতি’ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।
১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে দলিতদের অধিকার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ও বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়।
মূল মতভেদ:
আম্বেদকর মনে করতেন, হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাই অস্পৃশ্যতার মূল কারণ। তাই তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন।
গান্ধীজি বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক হলেও অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। তিনি দলিতদের ‘হরিজন’ বা ‘ঈশ্বরের সন্তান’ বলে আখ্যা দেন এবং পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করেন।
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুনা চুক্তি:
১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করে দলিতদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিলে আম্বেদকর তা সমর্থন করেন। গান্ধীজি এর প্রতিবাদে জেলে আমরণ অনশন শুরু করলে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে ‘পুনা চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পৃথক নির্বাচনের প্রথা বাতিল হয় এবং দলিতদের জন্য সাধারণ আসনে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়।
মূল্যায়ন: গান্ধীজি ও আম্বেদকরের মধ্যে মতভেদ থাকলেও উভয়েই দলিত সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে আন্তরিক ছিলেন।
৬. বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন সম্পর্কে কী জান?
উত্তর: বাংলার সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই চণ্ডাল বা নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়কে নীচস্থানীয়ভাবে দেখা হতো। তারা শিক্ষা, সম্পত্তি, সামাজিক অনুষ্ঠান ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। উচ্চবর্ণের শোষণ ও বৈষম্যের কারণে এই সম্প্রদায়ের মানুষ আত্মমর্যাদা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আন্দোলনের পথ বেছে নেন। এভাবেই জন্ম নেয় নমঃশূদ্র আন্দোলন।
(i) নমঃশূদ্র আন্দোলন ছিল বাংলার চণ্ডাল সম্প্রদায়ের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন।
(ii) প্রাচীন কালে এই সম্প্রদায়কে ‘চণ্ডাল’ বলা হতো; ১৯১১ সালের জনগণনায় তাদের নাম হয় ‘নমঃশূদ্র’।
(iii) তাদের আদি বসবাস ছিল পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায়।
(iv) ১৯০১ সালের জনগণনায় নমঃশূদ্রের সংখ্যা ১৮,৪৮,৪৮৩ জন এবং ১৯৩১ সালে ২০,৯৪,৯৫৭ জন; পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে ১৯০১ সালে ১৭.৬৬% এবং ১৯৩১ সালে ১৮.৯৪%।
(v) তারা মূলত কৃষিজীবী এবং অন্যান্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হলেও সমাজে মর্যাদা পেত না; শিক্ষা, সম্পত্তি, মন্দিরে প্রবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।
(vi) হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-৭৮ খ্রিঃ) ফরিদপুরের সফলাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করেন এবং ‘মতুয়া’ সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।
(vii) তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭ খ্রিঃ) শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জোরদার করেন; ৩৯৫২টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মেয়েদের ধাত্রীবিদ্যা ও নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(viii) পরবর্তীতে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (১৯২০-৯০ খ্রিঃ) নেতৃত্বে নমঃশূদ্র আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়।
(ix) রাজনৈতিকভাবে মতুয়া নেতৃত্ব উচ্চবর্ণ নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লিগের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখত।
আরও দেখো: রশিদ আলী দিবস কেন পালিত হয়েছিল