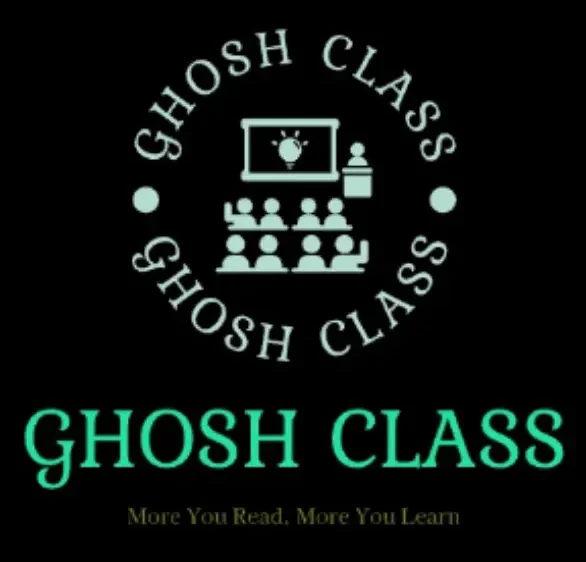এখানে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের প্রশ্ন উত্তর শেয়ার করা হলো। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা / ক্লাস 8 বাংলা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( হীরেন্দ্রনাথ দত্ত )
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের হাতে-কলমে প্রশ্ন উত্তর
১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
১.১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম লেখো।
উত্তর: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম হল অচেনা রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনে একযুগ।
১.২ কোন নামে তিনি সমধিক পরিচিত?
উত্তর: প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘ইন্দ্রজিৎ’ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।
২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।
২.১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন, এমন কয়েকজনের কথা আলোচনা করো।
উত্তর: শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আহ্বানে বহু কৃতী ব্যক্তি এসে শিক্ষাকর্মে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, আবার কেউ ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ও সুযোগে তাঁদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়:
রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁকে সংস্কৃত প্রবেশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেন। পরে তাঁর নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় নিযুক্ত হন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অনভিজ্ঞ হলেও তিনি ১৩১২ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অভিধান রচনা করেন। ১০৫ খণ্ডের এই অভিধান বাংলা ভাষার বৃহত্তম শব্দকোষ হিসেবে স্বীকৃত। অভিধান মুদ্রণ শেষ হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ মারা যান, কিন্তু হরিচরণবাবু শেষ পর্যন্ত একাগ্র সাধনায় কাজ সম্পূর্ণ করেন। জীবনের চল্লিশ বছর এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে তিনি বাঙালিজাতির সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং পরে বিশ্বভারতী তাঁকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধিতে সম্মানিত করে।
বিধুশেখর শাস্ত্রী:
প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং মূলত সংস্কৃত টোলের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পরিবেশে ও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় তিনি ধীরে ধীরে বহুভাষাবিদে পরিণত হন এবং ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।
ক্ষিতিমোহন সেন:
একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ, যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করেন। এর মাধ্যমে ভারতীয় জীবনসাধনার এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে তিনি নতুনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর কাজ ভারতীয় ভক্তি সাহিত্যচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।
মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী:
বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী মহারাজ, যিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। তাঁর এই মহানুভবতা ও আর্থিক সহায়তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমূল্য গ্রন্থ রচনায় সহায়ক হয়।
শান্তিনিকেতনের বিশেষত্ব ছিল—এখানে বিদ্যালয়কে শুধু বিদ্যাদানের কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যা-বিকিরণের স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের আহ্বান করেছিলেন, তাঁরা সবাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে বিদ্যালয়ের কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে যুক্ত হন। তাঁদের অবদান শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
২.২ ‘এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য…’ কোন কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে? তার বহুলাংশ ‘শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য’ বলে লেখক মনে করেছেন কেন?
উত্তর: এই মন্তব্যটি প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রবন্ধে করেছেন। এখানে সেই কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে, যেখানে অনেক সাধারণ প্রতিভাধারী ব্যক্তি শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে এসে নিষ্ঠা, মনোযোগ ও সাধনার মাধ্যমে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন।
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যোগ দেওয়া অনেকেই ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধিতে সমকক্ষদের মধ্যে সাধারণ; কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা, সর্বশক্তি প্রয়োগ এবং শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁদের কৃতিত্বকে বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের লুকানো সম্ভাবনা চিনতে পেরেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ, প্রেরণা ও দায়িত্ব দিয়েছিলেন।
শান্তিনিকেতন কেবল বিদ্যাদানের কেন্দ্র ছিল না; এটি বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যা-বিকিরণের স্থান ছিল। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করা, চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানো এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টিশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা—এসব ছিল এর মূল লক্ষ্য। এই অনন্য শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ বহু সাধারণ মানুষকেও অসাধারণ কীর্তি গড়তে সাহায্য করেছে।
তাই লেখকের মতে, তাঁদের এই অসাধারণ হয়ে ওঠার কৃতিত্ব যেমন ব্যক্তিগত সাধনার ফল, তেমনই বহুলাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য। শান্তিনিকেতনই তাঁদের গড়ে তুলেছিল এবং জীবনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা প্রকাশের পথ দেখিয়েছিল।
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের হাতে-কলমে প্রশ্ন উত্তর
২.৩ ‘আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম।’ লেখক এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেছেন?
উত্তর: প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত “হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শান্তিনিকেতন প্রথম দেশকে এই বার্তা দিয়েছিল যে বিদ্যালয় কেবল বিদ্যাদানের স্থান নয়—এটি বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যা-বিকিরণের কেন্দ্রও বটে। বিদ্যাকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ ও বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এবং বিদ্যার্জনের পথ সহজ করা—এই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য।
সে সময়ের কোনো বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় এই দায়িত্বকে এত গুরুত্ব দেয়নি, অথচ শান্তিনিকেতন তার সূচনালগ্ন থেকেই তা কার্যকর করেছে। শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্পর্ক, ও মুক্ত পরিবেশ—এসবের মাধ্যমে শান্তিনিকেতন সাধারণ মানুষকেও অসাধারণ হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে এর দান সত্যিই অপরিসীম।
২.৪ ‘আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিতে এড়াতে পারেনি।’ লেখক এ প্রসঙ্গে কাদের কথা স্মরণ করেছেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর: এই প্রসঙ্গে লেখক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ক্ষিতিমোহন সেনের কথা স্মরণ করেছেন।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এক সাধারণ জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যোগ্যতা চিনে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর হাতেই রচিত হয় শিশুদের উপযোগী প্রথম বাংলা বিজ্ঞানগ্রন্থমালা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ রচনার দায়িত্ব দেন, যা সম্পূর্ণ করতে তিনি জীবনের চল্লিশ বছর উৎসর্গ করেছিলেন।
বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ এক টোলপণ্ডিত। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় তিনি বহুভাষাবিদে পরিণত হন এবং ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে প্রথম সারিতে স্থান পান।
ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবনসাধনার এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে নতুন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন।
এঁদের জীবনের এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সাধারণ মানুষের মধ্যেও লুকিয়ে থাকা অসাধারণ প্রতিভাকে আবিষ্কার করে তা বিকশিত করার ক্ষমতা রাখত।
২.৫ “এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন।”- কাদের কথা বলা হয়েছে? কী-ই বা সেই দাবি? সেই দাবিপূরণে প্রাণপণে তাঁদের নিয়োজিত হওয়ারই-বা কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?
উত্তর: এখানে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যোগ দেওয়া কর্মবীর অধ্যাপকদের কথা বলা হয়েছে।
দাবিটি ছিল—আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও লুকানো প্রতিভাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকশিত করা, এবং শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের সমস্ত শক্তি ও সৃজনশীলতা শান্তিনিকেতনের জন্য উজাড় করে দিয়েছিলেন, তেমনই তিনি তাঁর সহযাত্রীদের কাছেও একইরকম নিষ্ঠা ও শ্রমের প্রত্যাশা করেছিলেন।
এই দাবিপূরণের প্রেরণা এসেছিল শান্তিনিকেতনের অনন্য পরিবেশ থেকে—যেখানে মুক্ত বিদ্যাচর্চা, সৃজনশীলতার স্বাধীনতা, এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল অপরিসীম। ফলে, এঁরা নিজেদের সাধ্যসীমা অতিক্রম করে প্রাণপণে জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন।
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের হাতে-কলমে প্রশ্ন উত্তর
২.৬ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছিল? প্রবন্ধ অনুসরণে তাঁর সারাজীবনব্যাপী সারস্বত-সাধনার পরিচয় দাও।
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পান। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কবিগুরু তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের পদে আহ্বান করেন। এভাবেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে হরিচরণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।
শান্তিনিকেতনে যোগদানের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দেন। কাজটি শেষ হলে ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনি শুরু করেন বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ সংকলন। এই মহাগ্রন্থের কাজ তিনি একার প্রচেষ্টায় চল্লিশ বছর ধরে (১৩১২–১৩৫২ বঙ্গাব্দ) সম্পন্ন করেন। অভিধানে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংযোজন তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।
আজীবন সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, বিশ্বভারতীর ‘ডি.লিট’ সম্মান ও ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি লাভ করেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।
২.৭ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের পরিচয় প্রবন্ধটিতে কীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।
উত্তর: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও হরিচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নানা দিক উঠে এসেছে। জমিদারি মহল্লায় কর্মরত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের অসাধারণতা উপলব্ধি করেন এবং সম্ভাবনা চিনে তাঁকে শান্তিনিকেতনে ডেকে আনেন।
রবীন্দ্রনাথ নিজের অসমাপ্ত ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ গ্রন্থের পরিসমাপ্তির দায়িত্ব হরিচরণকে দেন এবং পরে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ রচনার কাজেও নিয়োগ করেন। অর্থকষ্টে কলকাতায় ফিরে গেলে কবিগুরু তাঁর জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি সংগ্রহ করেন, যা তেরো বছর ধরে অব্যাহত ছিল।
এই অভিধান সম্পূর্ণ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেও, হরিচরণ আজীবন কবিগুরুর দেওয়া দায়িত্বকে দেবতার আশীর্বাদরূপে মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও গভীর সম্পর্কের পরিচয় স্পষ্ট হয়।
২.৮ “একক প্রচেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল।” কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? একে ‘বিরাট কাজ’ বলার কারণ কী?
উত্তর: উদ্ধৃত বাক্যে উল্লেখিত কাজটি হলো ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ সংকলন।
এটিকে ‘বিরাট কাজ’ বলা হয়েছে কারণ—
- কাজটির সময়কাল ছিল দীর্ঘ ৪০ বছর (১৩১২–১৩৫২ বঙ্গাব্দ)।
- এটি বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান, যা প্রথমে ১০৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।
- এককভাবে সংকলিত এই অভিধানে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক শব্দের জন্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ১৩৩০ বঙ্গাব্দে পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হলেও প্রায় দশ বছর ধরে সংশোধন ও পরিমার্জন চলেছে।
- বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় এর মুদ্রণ সম্পন্ন হয়, কিন্তু মূল শ্রম ছিল একমাত্র হরিচরণের।
এই বিশাল কাজ সম্পূর্ণ করতে যে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও একাগ্রতা প্রয়োজন, তার জন্যই প্রাবন্ধিক একে ‘বিরাট’ আখ্যা দিয়েছেন।
২.৯ “হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত”— শ্লোকটি কার লেখা? শ্লোকটি উদ্ধৃত করো।
উত্তর: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি একটি চৌপদী বা চার লাইনের কবিতা।
শ্লোকটি হলো—
“কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ! কোন গরতে?
বুঝেছি! শব্দ-অবধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে!”
২.১০ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত অভিধানটির নাম কী? গ্রন্থটির রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনার প্রসঙ্গ প্রাবন্ধিক কীভাবে স্মরণ করেছেন?
উত্তর: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত অভিধানটির নাম ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’।
রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ১৩১২ বঙ্গাব্দে বাংলা ভাষার এই বৃহত্তম অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে পান্ডুলিপি প্রস্তুত হলেও পরবর্তী দশ বছরে তাতে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। অবশেষে বিশ্বভারতী ছোট ছোট খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়।
পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসুসহ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং অসংখ্য শিক্ষিত অনুরাগী মুদ্রণ ব্যয়ের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। তবে মুদ্রণ শুরু হওয়ার আগেই প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরলোক গমন করেন। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত এই অভিধানের ছাপানোর কাজ শেষ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথও মৃত্যুবরণ করেন।
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের হাতে-কলমে প্রশ্ন উত্তর
২.১১ প্রাবন্ধিকের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রসঙ্গ প্রবন্ধে কীরূপ অনন্যতার স্বাদ এনে দিয়েছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার সময় হরিচরণবাবু অবসরপ্রাপ্ত হলেও লাইব্রেরির একটি ছোট কুঠুরিতে তাঁকে সর্বদা মনোযোগীভাবে কাজ করতে দেখতেন। কারণ তখনও ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এর ছাপানোর কাজ শেষ হয়নি।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্লোকটি তাঁর ক্ষেত্রে কতটা যথার্থ, প্রাবন্ধিক তা স্মরণ করেছেন। হরিচরণবাবুর ধ্যান, জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। অভিধান শেষ হওয়ার পরও তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকতেন। দৃষ্টি কমে যাওয়ায় সকলকে চিনতে না পারলেও কারও পরিচয় পেলে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন।
চল্লিশ বছরের সাধনায় অভিধান সংকলনের পরও তিনি ক্লান্ত হননি; বরং ছিলেন হাসিখুশি, প্রশান্তচিত্ত। যদিও প্রাবন্ধিক তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেননি, তবু তাঁর নিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
২.১২ “তিনি অভিধান ছাড়াও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন”— হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর: ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ — রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন; সংস্কৃত শেখার সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন; তিন খণ্ডে প্রকাশিত।
‘কবির কথা’ ও ‘রবীন্দ্র প্রসঙ্গ’ — সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবন বিষয়ক আলোচনা।
অনুবাদগ্রন্থ: ম্যাথু আর্নল্ডের ‘শোরাব রোস্তম’, ‘বশিষ্ট বিশ্বামিত্র’, ‘কবিকথা মঞ্জুষা’ — অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ।
ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ: সংস্কৃত প্রবেশ, পালি প্রবেশ, ব্যাকরণ কৌমুদী, Hints of Sanskrit Translation and Composition — ব্যাকরণ ও অনুবাদচর্চায় প্রসিদ্ধ।
‘রবীন্দ্রনাথের কথা’ — রবীন্দ্রনাথের জীবনের অজানা তথ্য প্রকাশ।
২.১৩ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনুরাগ কীভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা বিশদভাবে আলোচনা করো।
উত্তর: হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরাগ মূলত জন্ম নেয় হরিচরণবাবুর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থেকে। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে এক সাধকের মতো নিরলসভাবে কাজ করতে দেখে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত হন।
দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনায় তিনি ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ সংকলন করেন। কাজ শেষ হওয়ার পরও তাঁর মুখে ছিল প্রশান্তি ও তৃপ্তির ছাপ। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন— এটি এক সাধকের মনের প্রতিফলন।
প্রাবন্ধিকের কাছে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু একজন পণ্ডিত নন, বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক অনুরাগ সহকারে স্মরণ করেছেন।
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের অতিরিক্ত MCQ প্রশ্ন উত্তর
১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন—
① অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
② রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
③ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
④ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন—
① টোলের পণ্ডিত
② সেরেস্তার কর্মী
③ ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক
④ পুরোহিত
উত্তর: টোলের পণ্ডিত
৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত কোন গ্রন্থটি সংকলন করেন?
① চরিত্রমালা
② বঙ্গীয় শব্দকোষ
③ ইতিহাস-বিচিত্রা
④ বাংলা গানের ইতিহাস
উত্তর: বঙ্গীয় শব্দকোষ
৪. “গুরুদেব নিজে হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন।” — কথাটি কে বলতেন?
① বিধুশেখর শাস্ত্রী
② হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
③ ক্ষিতিমোহন সেন
④ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
উত্তর: ক্ষিতিমোহন সেন
৫. হরিচরণকৃত অভিধানের নাম—
① শব্দকোষ
② সংস্কৃত প্রবাদ
③ চলন্তিকা
④ বঙ্গীয় শব্দকোষ
উত্তর: বঙ্গীয় শব্দকোষ
৬. হরিচরণ মারা যান যত বছর বয়সে—
① পঁচানব্বই
② একানব্বই
③ বিরানব্বই
④ পঁচাত্তর বছরের পর
উত্তর: বিরানব্বই বছরের পর
৭. হরিচরণের অভিধানের পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয়—
① ১৩০৩ সালে
② ১৩১৩ সালে
③ ১৩২৩ সালে
④ ১৩৩০ সালে
উত্তর: ১৩৩০ সালে
৮. হরিচরণ অবসর নেন—
① ষাট বছরের পর
② পঁয়ষট্টি বছরের পর
③ পঁচাত্তর বছর
④ এগারো বছর
উত্তর: পঁচাত্তর বছরের পর
৯. অভিধান রচনার সূত্রপাত হয়—
① ১৩১২ সালে
② ১৩১৩ সালে
③ ১৩২২ সালে
④ ১৩১৪ সালে
উত্তর: ১৩১২ সালে
১০. গ্রন্থ সমাপ্তির পর হরিচরণ জীবিত ছিলেন—
① তের বছর
② পনেরো বছর
③ চোদ্দ বছর
④ এগারো বছর
উত্তর: চোদ্দ বছর
১১. হরিচরণ সম্পর্কিত শ্লোকটি রচনা করেন—
① রবীন্দ্রনাথ
② জীবেন্দ্রনাথ
③ বিধুশেখর
④ দ্বিজেন্দ্রনাথ
উত্তর: দ্বিজেন্দ্রনাথ
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্তর
১. শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
উত্তর: সবাই অসাধারণ না হলেও, নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও আত্মনিবেদন দিয়ে সাধনার মাধ্যমে অসাধারণ কাজ করেছেন।
২. লেখকের মতে ‘স্থান-মাহাত্ম্য’ বলতে কী বোঝায় এবং শান্তিনিকেতনের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য কী?
উত্তর: ‘স্থান-মাহাত্ম্য’ মানে শুধু স্থানীয় প্রাকৃতিক গুণ নয়, বরং মানুষের কাছ থেকে বড় দাবি করার অধিকার। শান্তিনিকেতন এই অধিকার অর্জন করেছে শিক্ষায় বিশাল দান ও ত্যাগের মাধ্যমে।
৩. শান্তিনিকেতন শিক্ষার ধারণায় কী নবত্ব এনেছিল?
উত্তর: বিদ্যালয় শুধু বিদ্যাদানের স্থান নয়, বরং বিদ্যাচর্চা, বিদ্যা-বিকিরণ এবং বিদ্যার্জনের পথ সুগম করার কেন্দ্র।
৪. রবীন্দ্রনাথ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী কাজে নিয়োজিত করেন এবং তখন তাঁর অবস্থা কেমন ছিল?
উত্তর: বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় নিয়োজিত করেন। তখন তিনি নবীন, অভিজ্ঞতাহীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও বড় রচনার অভিজ্ঞতা ছিল না।
৫. লেখক রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচনকে শেক্সপিয়ারের প্লট-নির্বাচনের সঙ্গে কেন তুলনা করেছেন?
উত্তর: যেমন শেক্সপিয়ার সাধারণ কাহিনিকেও প্রতিভার স্পর্শে মহৎ রচনায় রূপান্তর করতেন, রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের লুকানো সম্ভাবনাকে চিনে বড় কাজে লাগিয়েছেন।
৬. রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ক্ষিতিমোহন সেন কী কাজ করেন?
উত্তর: মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবন সাধনার বিস্তৃত একটি অধ্যায় পুনরুজ্জীবিত করেন।
৭. ক্ষিতিমোহন সেন নিজেই তাঁর বিকাশের কৃতিত্ব কাকে দেন?
উত্তর: গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে, যিনি নিজ হাতে তাঁদের গড়ে তুলেছিলেন এবং শেখা বিদ্যার যথাযথ ব্যবহার শিখিয়েছিলেন।
অষ্টম শ্রেণীর বাংলা
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের হাতে-কলমে প্রশ্ন উত্তর
সেট: ২
১. রবীন্দ্রনাথ মানুষের সম্ভাবনা যাচাই করার কী রীতি অনুসরণ করতেন?
উত্তর: প্রথমে দেখে নিতেন, দৈনন্দিন কাজ সেরে মানুষের মধ্যে ‘উদ্বৃত্ত’ কিছু আছে কিনা।
২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কোথায় দেখেন এবং কী প্রশ্ন করেন?
উত্তর: জমিদারি মহল্লা পরিদর্শনের সময় আমিনের সেরেস্তায়; প্রশ্ন করেন, রাত্রিতে কী করেন।
৩. হরিচরণের উত্তর শুনে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর সম্ভাবনা বুঝলেন?
উত্তর: তিনি জানালেন, সন্ধ্যায় সংস্কৃত চর্চা করেন ও একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে; রবীন্দ্রনাথ তাতে তাঁর উদ্বৃত্ত শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিনতে পারেন।
৪. হরিচরণ কখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন?
উত্তর: ১৩০৯ সনে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় এক বছরের মধ্যেই।
৫. রবীন্দ্রনাথ কোন সুবৃহৎ কাজের দায়িত্ব হরিচরণের হাতে দেন?
উত্তর: বঙ্গীয় শব্দকোষ (বৃহত্তম বাংলা অভিধান) রচনার কাজ।
৬. হরিচরণ কত সালে অভিধান রচনার কাজ শুরু ও শেষ করেন?
উত্তর: শুরু ১৩১২ সালে; পাণ্ডুলিপি শেষ ১৩৩০ সালে; মুদ্রণ শেষ ১৩৫২ সালে।
৭. আর্থিক অনটনে কলকাতায় চলে গেলে হরিচরণকে ফিরিয়ে আনতে কে উদ্যোগী হন এবং কীভাবে সহায়তা হয়?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে আবেদন করেন; মহারাজ মাসে ৫০ টাকার বৃত্তি দেন।
৮. রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে বৃত্তি প্রসঙ্গে কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?
উত্তর: ‘অভিধান শেষ হওয়ার আগে তোমার জীবননাশের শঙ্কা নেই’; ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়।
৯. অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
উত্তর: বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিটি শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ।
১০. হরিচরণের কর্মজীবনের শিক্ষণীয় দিক কী?
উত্তর: নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতায় জীবনের চল্লিশ বছর এক কাজে নিবেদন।
১১. হরিচরণ কী সম্মাননা লাভ করেন?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী স্বর্ণপদক, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সম্বর্ধনা, এবং বিশ্বভারতীর ‘দেশিকোত্তম’ (ডি.লিট) উপাধি।
১২. হরিচরণের মৃত্যু কবে হয় এবং শেষ বয়সে কেমন ছিলেন?
উত্তর: ১৯৫৯ সালে, ৯২ বছর বয়সে; শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ও মন প্রশান্ত ছিল।
আরও দেখো: দাঁড়াও কবিতার প্রশ্ন উত্তর